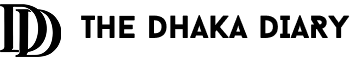'পুলিশের রিমান্ডে জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায় বিচারিক প্রক্রিয়ায় পদ্ধতিগত সহিংসতা'
প্রকাশিত: ৩০ মে ২০২৫, ২২:২১


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান বলেছেন, পুলিশের রিমান্ডে জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায় বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় একটি 'পদ্ধতিগত সহিংসতা'। এ ধরনের প্রক্রিয়া মৌলিক মানবাধিকারের পরিপন্থী এবং বিচারিক সংস্কারের দাবি অত্যন্ত জরুরি বলে তিনি মন্তব্য করেন।
বৃহস্পতিবার (২৯ মে) ঢাবির সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী অডিটোরিয়ামে ‘De-Cage Initiative’-এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত “Confessional Statement: Police Remand as a Procedural Violence in the Criminal Justice System” শীর্ষক সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে এসব কথা বলেন অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান।
তিনি বলেন, আইন অনুযায়ী, কাউকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করার বা নির্যাতনের অধিকার পুলিশের নেই। এটি একটি মৌলিক অধিকার। কিন্তু বাস্তবতা ও সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য আমাদেরকে এই প্রসঙ্গটি নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে।
অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বলেন, পুলিশি রিমান্ডকে অনেকেই নির্যাতনের সমার্থক হিসেবে দেখে থাকেন। অথচ সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রায়শই রিমান্ডে নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার করে। দেশের অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে রিমান্ড মানেই পুলিশি নির্যাতন।
স্বীকারোক্তির প্রকৃতি ও আইনি জটিলতা:
স্বীকারোক্তির বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেন, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেওয়া জবানবন্দিকে যদি 'স্বেচ্ছায়' দেওয়া বলে প্রত্যয়ন করা হয়, তবে সেটিকে আদালতে সত্য ধরে নেওয়া হয়। এরপর আসামিকেই প্রমাণ করতে হয় যে স্বীকারোক্তিটি মিথ্যা ছিল। তিনি প্রশ্ন তোলেন, "কেন একজন ব্যক্তি নিজেই নিজের বিরুদ্ধে অপরাধ স্বীকার করবে, যদি না তার মধ্যে অপরাধবোধ, শাস্তি হ্রাসের মতো কোনো কারণ থাকে।
তিনি আরও বলেন, উন্নত অনেক দেশে অপরাধ স্বীকার করলে সাজা হ্রাস পায়, কিন্তু বাংলাদেশের আইনে এমন কোনো বিধান নেই। ফলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কেবল বিবেকের তাড়নাতেই স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি আসতে পারে—তবে বাস্তবে তা বিরল।
নির্যাতনের সংস্কৃতি ও বিচার বিভাগের দায়:
তিনি সেকশন ১৬৪ কে 'বাইবেল' নয় উল্লেখ করে অধ্যাপক মাহবুবুর বলেন, “পুলিশের হেফাজতে থাকা অপরাধীদের একটি ছোট অংশই কেবল স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দেয়, যখন পলাতক বা জেল কাস্টডিতে থাকা ব্যক্তিরা তা করেন না। যখন আসামি পুলিশ হেফাজতে থাকে, তখনই কেন তার বিবেক জাগ্রত হয়? এর একমাত্র ব্যাখ্যা হলো—নির্যাতন।” তিনি দাবি করেন, বিচার বিভাগও এ ধরনের সহিংসতামূলক প্রক্রিয়াকে পদ্ধতিগতভাবে অস্বীকার করে আসছে বলে দায়ী করেন।
তিনি আরও বলেন, অনেক দেশে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হার যেখানে ৯০ শতাংশের বেশি, সেখানে বাংলাদেশে এটি মাত্র ১০ শতাংশ। এটি বিচারিক ব্যবস্থার অকার্যকারিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত।
তিনি সতর্ক করেন, অনেক দেশে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হার (conviction rate) শতকরা ৯০ ভাগ হলেও বাংলাদেশে এটি প্রায় ১০ ভাগ। সহিংসতা কখনোই বৈধতা পাওয়ার মতো কিছু নয়। 'ইমানসিপেটরি ভায়োলেন্স' বা মুক্তির জন্য সহিংসতার নামে সহিংসতা মহিমান্বিত করার প্রবণতা সমাজে সহিংসতার চক্র তৈরি করে। তিনি বলেন, "শুধু ‘সিভিল ডিসওবেডিয়েন্স’-এর নির্দিষ্ট সীমায় কিছু মাত্রার সহিংসতা স্বীকারযোগ্য হতে পারে, তবে এর বাইরে কোনো সহিংসতাকে বৈধতা দেওয়ার কোনো কারণ নেই।"
আইনি সংস্কার ও সমাধানের পথ:
অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান শান্তিপূর্ণ সংস্কারের ধারণাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেন। তিনি বলেন, কোনো ধরনের 'peaceful reform' কাজ করবে না এবং এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। ২০০৩ সালের BLAST মামলার রায় বা ২০১৩ সালের 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু নিবারণ আইন' সত্ত্বেও পুলিশি নির্যাতন বন্ধ হয়নি, বরং তার হাইপোথিসিস অনুযায়ী জোরপূর্বক গুমের প্রবণতা বেড়েছে।'
তিনি 'De-Cage Initiative'-এর প্রস্তাবিত ‘কুলিং পিরিয়ড’—অর্থাৎ রিমান্ডের পরপরই স্বীকারোক্তি না নেওয়া—কে একটি ভালো প্রস্তাব বলে উল্লেখ করেন।
অধ্যাপক রহমান বলেন, শুধুমাত্র আইনি সংস্কার বা কিছু এজেন্সির পরিবর্তন দিয়ে পরিস্থিতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। এর জন্য সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে, স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সহিংসতামুক্ত জুরিসপ্রুডেন্স ও রাজনৈতিক ডিসকোর্স দরকার। তার মতে, এসব প্রতিষ্ঠা করতে পারলে নতুন আইন প্রণয়ন না করেও অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব।
ম্যাজিস্ট্রেট, মানবাধিকার কর্মী, আইনজীবী ও ভুক্তভোগীর মন্তব্য :
সেমিনারে বক্তারা পুলিশের রিমান্ড প্রক্রিয়া, বিচার বিভাগের দুর্বলতা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের নানা দিক নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। সমাধানের জন্য একটি কার্যকর সংস্কার প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন যা শুধুমাত্র আইন দিয়ে নয়, রাজনৈতিক সদিচ্ছা, প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা, এবং সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সম্ভব।
ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ জাকির হোসেন জানান, রাজধানীর ৫২টি থানার বিপরীতে মাত্র ৩৭ জন ম্যাজিস্ট্রেট থাকায় প্রতিটি মামলায় যথাযথ সময় ও মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অতিরিক্ত কাজের চাপ এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অভাব বিচারিক ন্যায়বিচারের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে তিনি মত দেন। তিনি রিমান্ড ব্যবস্থার অপব্যবহার, প্রাথমিক তদন্তের অভাব এবং পুলিশের অদক্ষতা ও অসহযোগিতার বিষয়টিও তুলে ধরেন।
ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসেন ফৌজদারি মামলায় শতকরা ১০ ভাগের বেশি রিমান্ড দরকার হয় না বলে উল্লেখ করেন। অনেক সময় তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রাথমিক তদন্ত না করেই রিমান্ডের আশায় বসে থাকেন এবং রিমান্ডের জন্য দুই দিনের সময় নিয়ে কয়েক ঘণ্টাও ঠিকঠাক জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন না। দুর্বল প্রসিকিউশন এবং পুলিশের অসহযোগিতার কথাও তিনি তুলে ধরেন। সেকশন ১৬৪ ধারা সম্পর্কে ‘লিগ্যাল ডিফেক্ট’ এবং ফরেনসিক ইনভেস্টিগেশনের সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরেন।
সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী হেলাল উদ্দিন মোল্লা অভিযোগ করেন যে, অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশ গ্রেফতারের পরপরই আসামিকে অবৈধভাবে আটক রাখে এবং পরে কাগজে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার দেখানো হয়। তার ভাষ্যমতে, অধিকাংশ স্বীকারোক্তিই নির্যাতনের মাধ্যমে আদায় করা হয় এবং প্রায়শই পুলিশের তৈরি জবানবন্দিতে কেবল ম্যাজিস্ট্রেট স্বাক্ষর করেন। এছাড়া অনেক সময় ফর্মে থানা, মামলার নম্বর, ২৪ ঘণ্টার হিসাব কিছুই থাকে না এবং আসামি দুই-তিন দিন পরে কোনো রিমান্ড ছাড়াই হাজির করা হয়।
ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জিয়া উদ্দিন আহমেদ বলেন, পুলিশের মনস্তত্ত্ব হলো স্বীকারোক্তি আদায়ে সাফল্য খোঁজা, যা বিচারিক প্রমাণের ভিত্তিকে দুর্বল করে। তিনি সেকশন ১৬৪-এর অতি নির্ভরশীলতা কমিয়ে এর সঙ্গে corroborative evidence যুক্ত করার ওপর জোর দেন এবং তিন ঘণ্টার পরিবর্তে তিন দিনের ‘কুলিং পিরিয়ড’-এর প্রস্তাব দেন।
মানবাধিকার কর্মী মুশফিক জোহান বিচার ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি জানান, বর্তমানে ২৫০০-এরও বেশি ব্যক্তি দীর্ঘমেয়াদী সলিটারি কনফাইনমেন্টে রয়েছেন এবং অনেকেই ১০ বছরের বেশি সময় ধরে বন্দী। ‘লিভিং উইথ সোশ্যাল ডেথ’ ধারণা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, অনেক মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সমাজ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এসময় তিনি একজন ভিক্টিমের কথা উল্লেখ করেন যার মামলা হাইকোর্টে উঠতে বিশ বছর লেগে যায় এবং মুক্তি পাওয়ার পরেও তিনি একাকীত্বে ভুগছিলেন। তার বাবা-মা মারা যাওয়ার সময়ও তিনি তাদের দেখতে পারেননি। জোহান নির্যাতনকে মাধ্যম না করে প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার হওয়া উচিত বলে মনে করেন এবং নির্যাতন একেবারেই না থাকার প্রস্তাব দেন।
সেমিনারে ভুক্তভোগী আনোয়ার শংকর তার জীবনের মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, ২০০৫ সালে একটি অজ্ঞাত মামলায় তাকে গ্রেফতার করে অত্যাচার-নিপীড়ন মাধ্যমে জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়। পরে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং ২০২২ সালে মুক্তি পান। রিমান্ড পদ্ধতির ফলে ১৭ বছরের জেলজীবনে তার চারপাশের পৃথিবী বদলে যায়। তিনি রাষ্ট্র ও বিচারব্যবস্থার প্রতি প্রশ্ন রেখে বলেন, পুলিশের একটি ভুল সিদ্ধান্ত তার জীবন ধ্বংস করে দিয়েছে।
সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম মুসা একটি মামলার উদাহরণ তুলে ধরেন যেখানে একাধিক আসামির কাছ থেকে একই ধরনের স্বীকারোক্তি নেওয়া হয়, যা কপি-পেস্টের মতো ছিল। তিনি বলেন, রিমান্ড ছাড়াই পুলিশের হেফাজতে থেকে অনেক সময় স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়। তার মতে, শান্তিপূর্ণ সংস্কার এখানে যথেষ্ট নয়; বরং সুশীল সমাজে এই ইস্যুতে জনসচেতনতা গড়ে তোলার মাধ্যমে গণচাপ সৃষ্টি করাটাই প্রকৃত সমাধানের পথ হিসেবে ব্যক্ত করেন।